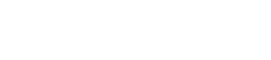শিশির মোড়ল
বাংলাদেশে স্বাস্থ্য সাংবাদিকতায় পরিবর্তন দৃশ্যমান। দুই দশক আগে স্বাস্থ্য নিয়ে যে পরিমাণ সংবাদ গণমাধ্যমে প্রকাশ পেত, এখন তার চেয়ে বেশি সংবাদ প্রচারিত হয়। শুধু পরিমাণে নয়, স্বাস্থ্য সাংবাদিকতার মানেও পরিবর্তন এসেছে। অতীতে স্বাস্থ্য সাংবাদিকতা ছিল মূলত হাসপাতালকেন্দ্রিক। হাসপাতালে শয্যার সংকট, রোগীর দুর্ভোগ, অবহেলায় রোগীর মৃত্যু, হাসপাতালে ছারপোকার উপদ্রব, হাসপাতাল থেকে আসামির পলায়ন, হাসপাতাল ভাঙচুর, ওষুধ চুরি, ভুল ওষুধ ব্যবহার- এসব নিয়েই সংবাদ ছাপা হতো। সাংবাদিকতা ছিল মূলত চিকিৎসাকে ঘিরে। সেই অবস্থা এখন আর নেই।
একটা সময় ছিল, যখন ভাবা হতো স্বাস্থ্য মানেই চিকিৎসার বিষয়। আর শুধু চিকিৎসকরাই এ বিষয়ে ভাবার, কথা বলার এখতিয়ার রাখেন। সেই অবস্থা থেকে উত্তরণ ঘটেছে। প্রয়োজনের চেয়ে কম হলেও এখন জনস্বাস্থ্য নিয়ে কথা, আলোচনা, বিতর্ক বেড়েছে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের বাইরে অন্য শাস্ত্রের ব্যক্তিও তাতে শামিল হয়েছেন। বৃহত্তর সমাজে স্বাস্থ্য নিয়ে জনসচেতনতা আগের চেয়ে বেড়েছে। চিকিৎসার বাইরে, হাসপাতালের বাইরে স্বাস্থ্য খাতে আর কী ঘটছে, সাধারণ মানুষ তা জানতে চায়। চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে গণমাধ্যমের পক্ষে তাই এক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকার কোনো সুযোগ ছিল না। যা কিছু স্বাস্থ্যে প্রভাব ফেলে তার সবকিছুতে গণমাধ্যম নজর দিতে চায়, দেওয়ার চেষ্টা করে।
গণমাধ্যমে এখন ‘স্বাস্থ্য বিট’ স্বীকৃত একটি বিট। দেশের প্রায় প্রতিটি বড়ো সংবাদপত্রে, সংবাদ এজেন্সিতে একজন নির্দিষ্ট প্রতিবেদক আছেন ‘স্বাস্থ্য’ কাভার করার জন্য। বেশ কয়েকটি টেলিভিশনেও স্বাস্থ্যবিষয়ক নির্দিষ্ট রিপোর্টার রয়েছেন। তারা প্রতিদিন দেশের সরকারি-বেসরকারি হাসপাতালে কী ঘটছে, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে কী সিদ্ধান্ত হচ্ছে, চিকিৎসকদের সংগঠনগুলো কী করছে, এর খোঁজ রাখছেন। স্বাস্থ্যপুষ্টি নিয়ে প্রায় প্রতিদিন সরকারি-বেসরকারি সংস্থা, গবেষণা প্রতিষ্ঠান নানা কর্মসূচির আয়োজন করে, যা তারা নিয়মিত কাভার করেন। পাশাপাশি জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর বিষয় বা স্বাস্থ্য খাতে অনিয়ম-দুর্নীতি নিয়ে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরি করছেন। বিশ্বের নামকরা জনস্বাস্থ্য বা চিকিৎসা সাময়িকীতে নতুন বৈজ্ঞানিক বা গবেষণা প্রবন্ধ ছাপা হচ্ছে কি না, এর খোঁজ রাখছেন এবং বাংলাদেশের জন্য প্রাসঙ্গিক হলে তা নিয়ে প্রতিবেদনও তৈরি করছেন।
স্বাস্থ্য যেহেতু একটি বিশেষায়িত বিষয় এবং এর সঙ্গে বিজ্ঞান, অর্থনীতি, ব্যবস্থাপনাসহ নানা বিষয় জড়িত, তাই সব রিপোর্টার বা সাংবাদিকের পক্ষে স্বাস্থ্যের খুঁটিনাটি বুঝে ওঠা প্রাথমিকভাবে একটু কঠিন হয়ে ওঠে। তবে এই সমস্যা দূর করার প্রয়াসও দেখা গেছে। একাধিক সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা, বিশ^বিদ্যালয় স্বাস্থ্যের নানা দিক নিয়ে এই বিটের সাংবাদিকদের জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। স্বাস্থ্য সাংবাদিকদের সংগঠন বাংলাদেশ হেলথ রিপোর্টার্স ফোরাম এসব আয়োজনে বিশেষ সহায়তা দেয়। এতে সাংবাদিকদের জ্ঞান ও দক্ষতা দুই-ই বেড়েছে। অতীতের যে কোনো সময়ের চেয়ে এখন অনেক নতুন বিষয় নিয়ে প্রতিবেদন ছাপা হয়।
স্বাস্থ্যে নতুন বিষয়ের কোনো শেষ নেই। স্বাস্থ্য ভালো রাখার, অটুট রাখার চেষ্টা মানুষের অনাদিকালের। স্বাস্থ্য ভালো রাখতে মানুষ প্রকৃতির ওপর নির্ভর করেছে, নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে। মানুষ এখনো তুলসীপাতার রস খাচ্ছে, একই সঙ্গে ডিএনএ সম্পাদনার চেষ্টাও করছে। স্বাস্থ্য ভালো রাখার এই চেষ্টা মানুষ কখনও এককভাবে করে, কখনও গোষ্ঠীবদ্ধভাবে, কখনও রাষ্ট্রীয়ভাবে, কখনও বৈশি^কভাবে করে। এসব চেষ্টা, উদ্ভাবন, উদ্যোগ নিয়ে নানা বিতর্কও হয়েছে। যেমন- এখন একটি বিতর্ক চলছে ব্যবহার উপযোগী তৈরি চিকিৎসা-খাদ্য বা আরইউটিএফ (রেডি টু ইউজ থেরাপিউটিক ফুড) নিয়ে। মারাত্মক তীব্র অপুষ্টির (সিভিয়ার অ্যাকুইট ম্যালনিউট্রিশন বা স্যাম) শিকার শিশুর চিকিৎসায় রোহিঙ্গা শিবিরগুলোয় আরইউটিএফ ব্যবহার করা হচ্ছে। দেশের একাধিক শীর্ষ পুষ্টিবিদ ও শিশুচিকিৎসক কাজটি ঠিক হচ্ছে না বলে মত দিয়েছেন।
বিংশ শতাব্দীর শুরুতে ম্যালেরিয়া, জন্ডিস, ফিতাকৃমির সংক্রমণের বড়ো ধরনের উদ্যোগ ছিল আফ্রিকায়। এটাই পরবর্তী সময়ে রোগ নিয়ন্ত্রণ কর্মকাণ্ডের ভিত্তি তৈরি করে। খ্রিষ্টান মিশনের সঙ্গে এশিয়া ও আফ্রিকার বহু অঞ্চলে কেন্দ্রভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে যায়। তখন ইউরোপের দেশগুলোয় পরিবেশ সুরক্ষা, নিরাপদ পানি সরবরাহ ও নগর পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থাকে জনস্বাস্থ্যের বিষয় বলে ভাবা হতো। ফরাসি উপনিবেশগুলোয় মহামারি প্রতিরোধে জোর দেওয়া হয়েছিল। ডেনমার্ক, নেদারল্যান্ডস, নরওয়ে ও সুইডেনে প্রসূতি সেবার উন্নতিতে কমিউনিটির ধাত্রীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা চালু করা হয়।
বৈশ্বিক বড়ো উদ্যোগ ছিল ১৯৪৮ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা প্রতিষ্ঠা। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নেতৃত্বে গত শতকের পঞ্চাশ, ষাট ও সত্তরের দশকে বিভিন্ন দেশে রোগ প্রতিরোধ উদ্যোগ ছিল উল্লেখযোগ্য। নির্দিষ্ট সময়ে বিশেষ রোগের প্রকোপ কমানোর বা রোগ নির্মূল করার কর্মসূচি হাতে নেওয়া হতে থাকে। প্রচারের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। গুটিবসন্তের জীবাণু এখন গবেষণাগারে, মানুষ থেকে মানুষে গুটিবসন্ত ছড়িয়ে পড়ার সর্বশেষ ঘটনা ঘটে ১৯৭৭ সালে। রোগ প্রতিরোধে সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি (ইপিআই) চালু হয় ১৯৭৪ সাল থেকে (বাংলাদেশে ১৯৭৯ সাল)। ‘২০০০ সালের মধ্যে সবার জন্য স্বাস্থ্য- এই বৈশ্বিক প্রতিশ্রুতি নেওয়া হয়েছিল ১৯৭৮ সালে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের আলমাআটাতে অনুষ্ঠিত প্রাথমিক স্বাস্থ্যবিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে।
আজও বিশ্বের সব মানুষের জন্য স্বাস্থ্য নিশ্চিত হয়নি। তবে নিশ্চিত করার চেষ্টাও থেমে নেই। অতীতের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে, ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে নতুন বিকল্প, নতুন পথের সন্ধান করছে বিশ্বসম্প্রদায়। তারই ধারাবাহিকতায় এসেছে সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষার (ইউনিভার্সাল হেলথ কাভারেজ) ধারণা। এই ধারণাকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়ার কাজে অগ্রভাগে আছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যে (এসডিজি) এই ধারণাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।
সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষার অর্থ-
১. প্রতিটি মানুষ উন্নতিসহায়ক, প্রতিরোধমূলক, আরোগ্যলাভকারী ও পুনর্বাসনমূলক স্বাস্থ্যসেবা পাবে।
২. এই সেবা হবে মানসম্পন্ন এবং মানুষ সেই মানসম্পন্ন সেবা পাবে তার প্রয়োজনের মুহূর্তে।
৩. সেবা পাওয়ার জন্য মানুষ তার সামর্থ্য অনুযায়ী খরচ করবে।
৪. অর্থের অভাবে মানুষ সেবাবঞ্চিত হবে না, সেবা নেওয়া থেকে বিরত থাকবে না এবং সেবার খরচ মেটাতে গিয়ে সে নিঃস্ব হয়ে পড়বে না। অর্থাৎ সেবা হবে আর্থিক ঝুঁকিমুক্ত।
স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার মূল্যবোধকে গুরুত্ব দিয়ে ২০০৫ সালে বিশ^ স্বাস্থ্য সংস্থার বার্ষিক সভা ওয়ার্ল্ড হেলথ অ্যাসেম্বলিতে সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ে সদস্য রাষ্ট্রগুলোয় কর্মসূচি হাতে নেওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। অনেকে মনে করেন, সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষার মূল ফোকাস স্বাস্থ্য খাতে অর্থায়নের ওপর। ২০১০ সালে বিশ^ স্বাস্থ্য সংস্থা যে বিশ্ব স্বাস্থ্য প্রতিবেদন প্রকাশ করে, তার শিরোনাম ছিল: ‘হেলথ সিস্টেমস ফাইন্যান্সিং: দ্য পাথ টু ইউনিভার্সাল কাভারেজ’।
২০১০ সালের ডিসেম্বরে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিবেদন প্রকাশের পরপরই এ বিষয়ে বাংলাদেশের গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশিত হয় (সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে চাই কার্যকর অর্থায়ন, প্রথম আলো, ১৩ জানুয়ারি ২০১১)। এরপর বিষয়টি সাংবাদিকদের কাছে স্পষ্ট করার উদ্যোগ নেয় রকেফেলার ফাউন্ডেশন। রকেফেলার ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিষয়ে সাংবাদিকদের জ্ঞান ও দক্ষতা বাড়াতে একটি প্রকল্প হাতে নেয়। ওই প্রকল্পের আওতায় বেশকিছু প্রশিক্ষণ হয়েছিল। সাংবাদিকদের ব্যবহারের জন্য ‘স্বাস্থ্য সন্ধান’ নামে গণমাধ্যম সহায়িকাও প্রকাশ করে পিআইবি।
পরবর্তী সময়ে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের জেমস পি গ্রান্ট স্কুল অব পাবলিক হেলথ সাংবাদিকদের নিয়ে কর্মশালা করে। তাতে অর্থায়ন করেছিল ইউএসএআইডি। এরকম উদ্যোগ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের হেলথ ইকোনমিক্স ইউনিটেরও আছে।
এরই ধারাবাহিকতায় আজকের এই উদ্যোগ। এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিষয়ে গণমাধ্যমে প্রতিবেদনের সংখ্যা ও মান বাড়ানো। কাজের সুবিধার্থে তিনটি বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা এগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা হয়েছে:
১. স্বাস্থ্য খাতে বৈষম্য: বর্তমান পরিস্থিতি কী, একজন সাংবাদিক কী চোখে দেখেন?
২. সামাজিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা কৌশল বা পদ্ধতি: এর সঙ্গে স্বাস্থ্যবিমার কী সম্পর্ক রয়েছে, প্রতিবেদন করার সুযোগ আছে কি?
৩. স্বাস্থ্য খাতে অর্থায়ন: অর্থায়ন কীভাবে হয়, সাংবাদিকের অনুসন্ধান করার কী আছে?
প্রতিটি বিষয় নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো। আলোচনার ভিত্তিতে নতুন প্রতিবেদনের ধারণা বের করাই এই অনুশীলনের মূল উদ্দেশ্য।
১. স্বাস্থ্য খাতে বৈষম্য
সিয়েরা লিওনে আজ যে শিশুটি জন্ম নিল, তার বেঁচে থাকার সম্ভাবনা ৪৬ বছর, এটাই তার প্রত্যাশিত গড় আয়ু। আর জাপানে জন্ম নিল যে শিশু, তার পৃথিবীতে বসবাসের সম্ভাবনা ৮৪ বছর। জন্মের দিনেই ঠিক হলো যে, পৃথিবীর এক প্রান্তে জন্ম নেওয়া শিশু অন্য প্রান্তের জন্ম নেওয়া শিশুটির চেয়ে ৩৮ বছর কম বাঁচবে। প্রায় একজীবনের পার্থক্য। একই সময়ে একই পৃথিবীতে খারাপ ও ভালোর সহাবস্থান। (মাইকেল মারমোট, দ্য হেলথ গ্যাপ, ২০১৫)
স্বাস্থ্যে এই বৈষম্য শুধু ধনী আর দরিদ্র দেশের মধ্যে নয়। একটি দেশের অভ্যন্তরেও এই বৈষম্য দেখা যায়। স্বাস্থ্য খাতে মাথাপিছু ব্যয় সবচেয়ে বেশি যুক্তরাষ্ট্রে। এই দেশে শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গের স্বাস্থ্যে ব্যাপক পার্থক্য আছে। কৃষ্ণাঙ্গদের মধ্যে মাদকাসক্তি, হৃদরোগ, স্থূলতা বেশি।
শুধু যুক্তরাষ্ট্রে নয়, এই বৈষম্য বা পার্থক্য বাংলাদেশেও আছে। বাংলাদেশে সবচেয়ে ধনিক শ্রেণির পাঁচ বছরের কম বয়সি ২৬ শতাংশ শিশুর বয়সের তুলনায় উচ্চতা কম (স্টানটেড)। সবচেয়ে দরিদ্র শ্রেণির মধ্যে এই হার প্রায় দ্বিগুণ, ৫৪ শতাংশ। পাঁচ বছরের কম বয়সি শিশু মৃত্যুহার প্রতি হাজারে ধনিক শ্রেণিতে ৪৩ আর দরিদ্র শ্রেণিতে ৮৫।
বাংলাদেশে প্রসব-পূর্ববর্তী চারবার প্রসূতি সেবা পায় দরিদ্র পরিবারের ৭ শতাংশ গর্ভবতী, ধনিক শ্রেণির মধ্যে এই হার ৪৭ শতাংশ। প্রসবকালে দক্ষ প্রসবকর্মীর সহায়তা ধনিক শ্রেণির প্রসূতিরা বেশি পায়। অন্যদিকে প্রসবকালে গ্রামের প্রসূতিরা শহরের প্রসূতিদের তুলনায় দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মীর সহায়তা কম পায়।
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে, শিক্ষা পাওয়া না পাওয়ার বিষয়টি স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে বৈষম্য তৈরি করে। শিক্ষিত মায়েরা স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে নিরক্ষর মায়েদের চেয়ে এগিয়ে। শিক্ষিত মায়েদের মধ্যে প্রসবপূর্ব সেবা গ্রহণ, জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারের হার বেশি। মা নিরক্ষর হলে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে শিশুর স্বাস্থ্যের ওপর। নিরক্ষর মায়েদের শিশু কম টিকা পায়, নিরক্ষর মায়েদের মধ্যে শিশু মৃত্যুহার বেশি।
স্বাস্থ্য ব্যয়ের ক্ষেত্রেও বৈষম্য আছে। সর্বশেষ বাংলাদেশ ন্যাশনাল হেলথ অ্যাকাউন্টসের হিসাব অনুযায়ী, মোট স্বাস্থ্য ব্যয়ের ৪৬ শতাংশ ব্যয় হয় ঢাকা বিভাগে। সিলেট ও বরিশাল বিভাগে ব্যয় হয় ৪ শতাংশ করে। ধারণা হতে পারে ঢাকায় মানুষ বেশি তাই মোট স্বাস্থ্য ব্যয়ও বেশি। কিন্তু হিসাবের আরও একটু গভীরে গেলে বৈষম্য ধরা পড়ে। ঢাকা বিভাগে মাথাপিছু বার্ষিক ব্যয় ৩ হাজার ৮৫৬ টাকা। দেশে এটাই সবচেয়ে বেশি। মাথাপিছু ব্যয় সবচেয়ে কম রংপুর বিভাগে। এই বিভাগে মাথাপিছু বার্ষিক স্বাস্থ্য ব্যয় ১ হাজার ৫০৩ টাকা।
এই তালিকা অনেক দীর্ঘ করা যায়। শিক্ষা, পেশা, পরিবারের আয়, অবস্থান, জেন্ডারÑ এসব সামাজিক বিষয় (সোশ্যাল ডিটারমিনেন্টস) বৈষম্য তৈরিতে ভূমিকা রাখে।
এখন প্রশ্ন হচ্ছে- বৈষম্য কেন হয়? বৈষম্য কি কেউ তৈরি করে, নাকি বৈষম্য আপনা-আপনি সৃষ্টি হয়। সরকার সব উপজেলায় একটি করে উপজেলা হাসপাতাল তৈরি করেছে। এক্ষেত্রে সরকার কোনো বৈষম্য করেনি। কিন্তু রাজধানীর পাশের সাভার উপজেলার যে কোনো প্রান্তের রোগীর পক্ষে উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পৌঁছানো সহজ, সেবা পেতে কষ্ট হয় না। অন্যদিকে হাওড় এলাকার বা তিস্তাপারের মানুষকে অনেক কষ্টে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পৌঁছাতে হয়। তাই এদের মধ্যে সেবা গ্রহণের হার কম, স্বাস্থ্য সূচকে এরা পিছিয়ে। প্রবেশগম্যতা এখানে বৈষম্য তৈরি করেছে।
বরিশাল বিভাগে চিকিৎসকের শূন্যপদ সবচেয়ে বেশি। এর অর্থ- কর্মস্থলে উপস্থিত চিকিৎসকের ওপর রোগীর চাপও বেশি। তুলনামূলকভাবে রোগী কম থাকায় ঢাকার কাছে যে কোনো উপজেলায় একজন চিকিৎসক যে মানের সেবা দিতে পারেন, বরিশাল বা ভোলার উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সেটা সম্ভব হয় না। সেবার মান এখানে বৈষম্য তৈরি করেছে। সেবার মানে এই বৈষম্য হয়েছে ব্যবস্থাপনার ত্রুটির কারণে।
বৈষম্যের তালিকা দীর্ঘ করার পাশাপাশি এ নিয়ে আলোচনা প্রলম্বিত করা যায়। তবে এক্ষেত্রে মূল বক্তব্য হচ্ছে, স্বাস্থ্য খাতে বৈষম্য নিয়ে রিপোর্ট করার সুযোগ আছে। বেশি রিপোর্ট হলে বৈষম্য দূর হওয়ারও সম্ভাবনা বাড়বে।
২. সামাজিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা কৌশল বা পদ্ধতি
প্রতিবেশী অনেক ক্ষেত্রে নির্ধারণ করে দেয় ব্যক্তির স্বাস্থ্য ভালো না খারাপ থাকবে। ব্যক্তি সমাজ বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে পারে না। সবার স্বাস্থ্য ভালো রাখার মধ্য দিয়েই ব্যক্তির স্বাস্থ্য ভালো থাকে। ব্যক্তির স্বাস্থ্য ভালো রাখার ক্ষেত্রে সমাজের ভূমিকা অনেক। সমাজ যত বেশি স্বাস্থ্য সচেতন হবে, ব্যক্তি তত উন্নত স্বাস্থ্যের অধিকারী হবে। সমাজ যেহেতু ব্যক্তির সমষ্টি, তাই সব ব্যক্তির স্বাস্থ্য ভালো রাখার মধ্য দিয়ে সমাজ সুস্থ থাকবে- সাদামাটাভাবে এটাই সামাজিক স্বাস্থ্য সুরক্ষার মূলকথা।
আমরা যদি পাড়া-প্রতিবেশীর দিকে তাকাই, তাহলে সমাজের এই ভূমিকা দেখতে পাই। প্রসূতিকে জরুরি চিকিৎসার জন্য গ্রামের মানুষ এখনো নৌকা দিয়ে, জনবল দিয়ে সহায়তা করে। আবার জাতীয় টিকাদান কর্মসূচিতে হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবক অংশ নেন। এর পেছনে কাজ করে মূল্যবোধ।
এই মূল্যবোধই তৈরি করে সামাজিক পুঁজি বা সোশ্যাল ক্যাপিটাল। সমাজের এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষার আলোচনায় স্থান পায় না। এর সঙ্গে অর্থের সম্পর্ক কম।
সামাজিক স্বাস্থ্য সুরক্ষার ধারণা মূলত কতগুলো মূল্যবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত: ন্যায্যতা (Equity), সংহতি বা ঐক্য (Solidarity), সামাজিক ন্যায়বিচার (Social justice)- এগুলো অন্যতম। কিন্তু সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষার আলোচনায় ব্যক্তি যখন অসুস্থ হয়ে পড়ে, তখন সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে চিকিৎসার খরচ কীভাবে মিটবে বা অর্থায়ন কীভাবে হবে এবং ব্যক্তি কী কী সুযোগ-সুবিধা (বেনিফিট প্যাকেজ) পাবে, সেটাই প্রধান বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।
সামাজিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা ব্যবস্থার মূল বক্তব্য হচ্ছে, রোগগ্রস্ততার ঝুঁকি সবার আছে। এই ঝুঁকি মোকাবিলায় সমাজের সবাই এগিয়ে আসবে, তৈরি করবে একটি তহবিল। যার চিকিৎসা দরকার হবে, সে ওই তহবিলের সহায়তা পাবে। অর্থ দেবে সবাই, কিন্তু সহায়তা পাবে যার দরকার শুধু সে-ই।
সহায়তার নানা ধরন
ট্যাক্স বা কর:
মানুষ সরকারকে ট্যাক্স বা কর দেয়, সেই ট্যাক্সের টাকা সরকার স্বাস্থ্যের জন্য খরচ করে বা করতে পারে। ব্যক্তির আয়, সম্পত্তি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, করপোরেট লাভ- এসবের ওপর সরকার নির্দিষ্ট কর ধার্য ও গ্রহণ করে। এগুলো সরাসরি বা প্রত্যক্ষ কর। আবার কিছু পরোক্ষ করও আছে। পণ্য বা সেবা পেতে গেলে ব্যক্তিকে তা পরিশোধ করতে হয়। যেমন- পাপ কর বা সিন ট্যাক্স। অনেক দেশে সিগারেট, বিড়ি বা অন্য তামাকজাতীয় পণ্যের ক্ষেত্রে এই ট্যাক্স প্রযোজ্য। ফিলিপাইনে সিন ট্যাক্সের ৮০ শতাংশ দেওয়া হয় জনগণের স্বাস্থ্যসেবায়। দুই ধরনের ট্যাক্সের বাইরে স্বাস্থ্য খাতে সরকারের বার্ষিক বরাদ্দ থাকে। এর বাইরে সরকার গর্ভবতী নারী বা কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্য খাতে বিশেষ বরাদ্দ করতে পারে। জাতীয় কোনো স্বাস্থ্যবিমা কর্মসূচি থাকলে সেখানে বার্ষিক বরাদ্দ বা শ্রেণিবিশেষের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দিতে পারে।
বেতন পেলেই স্বাস্থ্য কর:
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মচারীদের প্রতিমাসের বেতন থেকে বেতনের পরিমাণ অনুযায়ী নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা চিকিৎসায় ব্যয় করার জন্য কেটে রাখে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। বিশ^বিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মচারীরা রোগের ঝুঁকিতে আছে- এই বিবেচনা থেকে তাদের বেতন কাটা হয় না, কাটা অংশটা জমানো হয় ভবিষ্যতে অসুস্থ হয়ে পড়লে চিকিৎসার খরচ মেটাতে। জমা যা-ই হোক, তহবিল থেকে একবারে সর্বোচ্চ পাঁচ লাখ টাকা পেতে পারেন শিক্ষক-কর্মচারীরা। বাংলাদেশে আরও অনেক প্রতিষ্ঠানে এই ধরনের ব্যবস্থা চালু আছে।
ফিলিপাইনে এটি আইন করে সবার জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। অর্থাৎ যারা নিয়মিত বেতন পান তাদের স্বাস্থ্য কর দেওয়া বাধ্যতামূলক। করের পরিমাণ নির্ধারিত হয় বেতনের ওপর। এই কর পরিশোধ করেন চাকরিদাতা। কোনো ড্রাইভার যদি নিয়মিত বেতন পান, তাহলে তার স্বাস্থ্য করও পরিশোধ করতে হয় ওই ড্রাইভার যার গাড়ি চালান তাকে। তবে অসুস্থ হলে গাড়ির মালিক ও ড্রাইভার একই মানের সেবা পান।
বিমা ব্যবস্থা:
প্রতিমাসে বা বছরে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ একটি তহবিলে জমা হয় এবং শর্ত অনুযায়ী সেই অর্থ ব্যক্তির চিকিৎসায় বা স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ব্যয় করা হয়। প্রতিমাসের বা বছরের প্রদেয় অর্থের পরিমাণ (প্রিমিয়াম) কত হবে, তহবিল ব্যবস্থাপনা কে করবে, বেনিফিট প্যাকেজে কী থাকবে- এসবই চুক্তির মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, সমবায় সমিতি, ট্রেড ইউনিয়ন বা ব্যবসায়িক কোম্পানি এর ব্যবস্থাপনায় থাকতে পারে। বাংলাদেশে সবার জন্য এই বিমা ব্যবস্থা চালু করা যায় কি না, তা নিয়ে বেশি আলোচনা হচ্ছে।
এই তিনটি ক্ষেত্রে বাংলাদেশে কী হচ্ছে, তা অনুসন্ধান করার সুযোগ আছে। সাংবাদিকরা চাইলে এক্ষেত্রে ব্যাখ্যামূলক রিপোর্টিং করতে পারেন।
৩. স্বাস্থ্য খাতে অর্থায়ন
সর্বশেষ হিসাব বলছে, দেশের মানুষের স্বাস্থ্যসেবায় বছরে ৪৫ হাজার কোটি টাকা খরচ হয়। মাথাপিছু বার্ষিক স্বাস্থ্য ব্যয় ৩৭ ডলার বা ২ হাজার ৮৮২ টাকা।
স্বাস্থ্য ব্যয়ের সবচেয়ে বড়ো অংশ আসে মানুষের পকেট থেকে। মোট স্বাস্থ্য ব্যয়ের ৬৭ শতাংশ মানুষ নিজে খরচ করে। সরকার মোট খরচের ২৩ শতাংশ বহন করে। সরকারের এই খরচের মধ্যে আছে উন্নয়ন প্রকল্প এবং নিয়মিত বার্ষিক খরচ (বেতনভাতা ইত্যাদি)। উন্নয়ন সহযোগী ও দাতাদের অর্থের পরিমাণ ৭ শতাংশ। আর দাতব্য প্রতিষ্ঠানসহ এনজিওগুলোর অবদান ৩ শতাংশ।
হিসাব বলছে, স্বাস্থ্যের জন্য মানুষ নিজের পকেট থেকেই বেশি খরচ করে। মাথাপিছুর হিসাবের মধ্যে কিছু সত্য লুকানো অবস্থায় আছে। ধনী ব্যক্তি সামান্য অসুখে পাঁচতারা হাসপাতালে সেবা নেন, তার বার্ষিক খরচ অনেক বেশি। আর দরিদ্র যে, সে সামান্যই খরচ করে। সবচেয়ে ধনিক ও দরিদ্র শ্রেণির হিসাব পাওয়া গেলে বোঝা যাবে আসলেই দরিদ্র মানুষ কত খরচ করে বা করতে পারে।
মানুষ এই টাকা পায় কোথা থেকে। মানুষ নিজের উপার্জন থেকে ব্যয় করে। যার উপার্জন নেই, সে সম্পত্তি বিক্রি করে বা ধারদেনা করে। এই ধারদেনা বা সম্পত্তি বিক্রি করে চিকিৎসার আকস্মিক ব্যয় মেটাতে গিয়ে প্রতিবছর বহু মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে চলে যায়। দারিদ্র্য স্বাস্থ্যহানি ঘটায়। দারিদ্র্যসীমার নিচে আসা মানুষ নতুন সমস্যায় পড়ে।
সরকার দুইভাবে স্বাস্থ্য খাতে অর্থ খরচ করে। একটি রাজস্ব বাজেটের মাধ্যমে। এতে মূলত সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতনভাতা নিশ্চিত করা হয় এবং গতানুগতিকভাবে প্রতিবছর এই বাজেট বাড়ে। অন্যটি উন্নয়ন বাজেট। এটি এখন হচ্ছে মূলত স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাত উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে। বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনায় (অপারেশন প্ল্যানে) সরকার অর্থ বরাদ্দ দিচ্ছে। এসব কর্মপরিকল্পনায় দাতা সংস্থারও অর্থ আছে।
দাতারা স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাত উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে অর্থ দেয়। আবার কিছু ক্ষেত্রে বিশেষ প্রকল্প বাস্তবায়নেও অর্থ দেয়। বাকি অংশটা আসে এনজিও, দাতব্য প্রতিষ্ঠান ও বিমা প্রতিষ্ঠান থেকে।
কোথায় খরচ হয়
মানুষ বেশি খরচ করে ওষুধের পেছনে। চিকিৎসা খাতে ব্যক্তির মাথাপিছু যে ব্যয়, তার ৭০ শতাংশ চলে যায় ওষুধ কিনতে। হাসপাতাল বা ক্লিনিক থেকে নিরাময়মূলক সেবা পেতে ১১.৫ শতাংশ খরচ হয়। হাসপাতালের বহির্বিভাগে খরচ করে ১০ শতাংশ। ৮.২ শতাংশ পরীক্ষা-নিরীক্ষায় খরচ হয়। অন্যান্য খাতে দশমিক ৮ শতাংশ।
প্রমাণ বা সফল উদাহরণভিত্তিক সিদ্ধান্ত
স্বাস্থ্যে অর্থায়ন জটিল প্রক্রিয়া এবং অগ্রাধিকার ঠিক করা কঠিন। ২০ কোটি টাকার যন্ত্র কেনা জরুরি না টিকা দেওয়া জরুরি। জনবল বাড়ানো দরকার, না হাসপাতাল ভবন নির্মাণ দরকারÑ কোনটা আগে? সম্পদের সীমাবদ্ধতা আছে। সুতরাং অর্থ ব্যয় বা বিনিয়োগের আগে দেখতে হবে দেশে বা বিদেশে এক্ষেত্রে ভালো উদাহরণ কি আছে।
সরকার কী করছে
সরকার সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করার কথা বলছে। পাঁচ বছর মেয়াদি (২০১৭-২০২১) চলমান স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাত উন্নয়ন কর্মসূচির দলিলে এই নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। এর আগে হেলথ ইকোনমিক্স ইউনিট ২০ বছর মেয়াদি স্বাস্থ্যসেবা অর্থায়ন কৌশলপত্র (২০১২-২০৩২) তৈরি করেছিল। সেই কৌশলপত্রের দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য ছিল সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা।
ওই কৌশলপত্রে স্বাস্থ্য খাতে অর্থায়নের বেশকিছু চ্যালেঞ্জের উল্লেখ আছে। সেগুলো হচ্ছে:
১. স্বাস্থ্য খাতে সম্পদের স্বল্পতা।
২. স্বাস্থ্যসেবায় অর্থ বরাদ্দ ও ব্যবহারে অন্যায্যতা।
৩. বরাদ্দকৃত সম্পদ ব্যবহারে অদক্ষতা।
ওই দলিলে পকেট থেকে নগদ ব্যয় (Out of Pocket Expenditure) কমানোর লক্ষ্যে তিনটি কৌশলগত উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়েছিল:
১. কার্যকর স্বাস্থ্যসেবার জন্য আরও সম্পদের ব্যবস্থা করা।
২. স্বাস্থ্যসেবার ন্যায্যতা জোরদার করা এবং দরিদ্র ও অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর জন্য স্বাস্থ্য সুবিধা বাড়ানো।
৩. সম্পদের বরাদ্দ ও ব্যবহারে দক্ষতা বৃদ্ধি।
এই কৌশলপত্র তৈরির সময় পকেট থেকে নগদ ব্যয় ছিল ৬৩ শতাংশ। আর এখন তা বেড়ে ৬৭ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। উলটো কেন হলো, এর পর্যালোচনা হওয়া দরকার।
সরকারি ব্যবস্থাপনায় স্বাস্থ্যবিমা চালু করার একটি দিশারি প্রকল্প হাতে নেওয়ার কথা এই কৌশলপত্রে উল্লেখ আছে। স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচি নামের ওই দিশারি প্রকল্প ২০১৬ সালের মধ্যে শেষ হওয়ার কথা ছিল। বাস্তবে টাঙ্গাইলের তিনটি উপজেলায় দিশারি প্রকল্পটি শুরু হয়েছিল ২০১৬ সালে। এখনো তা শেষ হয়নি।
শেষের গল্প
সদরঘাটেই বেড়ে উঠেছিলেন ভোলার তসলিম মিয়া। মুটেগিরি করে বেড়ে ওঠা। বিয়ে। ছেলে ক্লাস এইট, মেয়ে কলেজে। কলার খোসায় পা পিছলে যায় সুঠামদেহী তসলিমের। মেরুদণ্ডে আঘাত। আর কোনোদিন সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারেননি। চিকিৎসা ব্যয় মেটাতে প্রথমে মেয়ের, পরে ছেলের পড়ালেখা বন্ধ। পরিবারটি নিঃস্ব।
যদি মুটেদের সংগঠন তসলিমের পাশে দাঁড়াত, যদি স্বাস্থ্যবিমা থাকত, যদি তসলিমের চিকিৎসায় পরিবারকে কোনো খরচ করতে না হতো, তাহলে গল্পের শেষটা অন্যরকম হতে পারত। সেই অন্যরকম গল্প লেখার কথাই বলে সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা।
লেখক: বিশেষ প্রতিনিধি, প্রথম আলো